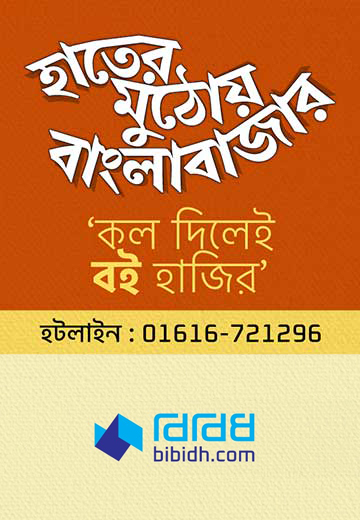কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার দুই দশক ধরে লিখছেন গল্প-উপন্যাস। তার লেখায় রয়েছে অনুসন্ধান, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের খনন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘তালাশ’ বোদ্ধামহলের প্রশংসা অর্জন করে। এ বইয়ের জন্য পান ‘এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড’ও। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নূর কামরুন নাহার
তালাশ আপনার আলোচিত একটি বই। প্রশংসিতও। এই উপন্যাস ‘এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড’ পেল। এ সময়েও এই বই, বইয়ের চরিত্র এবং ঘটনাগুলো আপনাকে কেমন করে ভাবায়? মনে হয় এরা সময়ের প্রতিনিধি? উপন্যাসটায় আরো কিছু করা যেত, এমন কোনো ভাবনাও কি তাড়িত করে?
চিত্রশিল্পী নাসরীন বেগমের কথা দিয়ে শুরু করি। তিনি ‘তালাশ’ সম্পর্কে ফেসবুকে লিখেছেন ‘আমরা তো ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী ধারাবাহিক সময় পেরিয়ে আজকের বাস্তবতা দেখছি। নতুন প্রজন্ম তো কিছুই জানে না।… এ ধরনের বই বারবার পড়তে হয়, কারণ বাস্তব সময়ের সঙ্গে অনেক নতুন নতুন উপলব্ধি, বোধ জন্মে।’ নাসরীন বেগমের মন্তব্যটি পড়ে আমি চমকে গেছি। প্রকাশের পর একটা বই পাঠকের কাছে নতুন করে জন্ম নেয় শুনেছি। কিন্তু একই পাঠকের কাছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বোধের, উপলব্ধির জন্ম দেওয়ার চিন্তাটা সত্যিই অভিনব। আমার মনে হয়, এমন দারুণ চিন্তা লেখকের চেয়ে পাঠকের পক্ষেই করা সম্ভব।
১৬ বছর আগে, ২০০৪ সালে মাওলা ব্রাদার্স থেকে ‘তালাশ’ ছাপা হয়েছে। সত্যিকারে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে বইটার সঙ্গে। ‘উপন্যাসটায় আরো কিছু করা যেত কি না’ এ প্রশ্নের জবাবে বলি, সে ধরনের কোনো তাড়না আমি অনুভব করি না। তবে হ্যাঁ, বাজারে এখন ‘তালাশ’-এর যে সংস্করণ আছে, তা ২০১৬ সালের সম্পাদিত এডিশন।
‘এশিয়া লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড’ সত্যিকারেই আমার জন্য একটি চমক। তার আগে ২০১৬ সালে ‘তালাশ’-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ে সিং হি জন (‘তালাশ’-এর কোরিয়ান অনুবাদক) আমাকে ইমেইল করেন। তাদেরও যুদ্ধের ভয়াল অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষ করে তাদের আগের জেনারেশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভুক্তভোগী ‘কমফোর্ট উইমেন’। যারা প্রথমত যুদ্ধের সময় জাপানি সৈন্যদের হাতে নির্যাতিত হয়, পরে যুদ্ধোত্তরকালে নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছে নিজের দেশে। যেমনটা আমাদের দেশের বীরাঙ্গনাদের বেলায় ঘটেছিল। ‘তালাশ’ কোরীয়দের আবেগকে ছুঁতে পেরেছে ভেবে আমি তখন খুব আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম। আর তখনই আমি উপলব্ধি করি, ‘তালাশ’-এর ঘটনা, চরিত্র একটা নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের ফ্রেমে আটকে নেই, পৃথিবীর আরেক প্রান্তের যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের মনেও তা গভীর ছাপ ফেলতে পারে।
তালাশে আমরা তো একটা তালাশই দেখি। সেই তালাশ ইতিহাস, ইতিহাস বিবর্তনের এবং একটা সময় ও যুদ্ধের। এই তালাশ কতটা জিইয়ে রেখেছে উপন্যাসটি?
হ্যাঁ ‘তালাশ’ উপন্যাস সত্যিকারেই খোঁজাখুঁজি তালাশ। তালাশ জনপদে, জনপদের বাইরে, ব্যাংকারে, স্মৃতিতে, বিস্মৃতিতে। বীরাঙ্গনারা যেন শুধু পরিসংখ্যানে আটকে না থাকে। উপন্যাসে তালাশের শেষ নেই, এই অশেষ।
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে গেলে মরা একটা দীর্ঘশ্বাস আর হতাশার সুর দেখি, বলা হয় আমাদের উপন্যাস সেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে আনতে পারেনি, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?
‘আমাদের উপন্যাস সেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে আনতে পারেনি’ এ কথা থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে না। আরেকটা কথা, আমি মুক্তিযুদ্ধ উপজীব্য করে উপন্যাস লিখেছি বলে, মুক্তিযুদ্ধের তাবৎ উপন্যাস মূল্যায়নের যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখি, এ রকম আশা করাটা ঠিক হবে না।
উপন্যাসের মুক্তি চরিত্রটি যেন নিজেকেই দেখা হয়। মনে হয় আমিই মুক্তি? একাত্তরে জন্ম নিয়েও আমাদের যাদের যুদ্ধের কোনো স্মৃতি নেই, তাদের কাছে এ চরিত্র যেন অন্য এক মেসেজ নিয়ে আসে। আপনি কি তাই চেয়েছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটা বার্তা দিতে?
আমি সচেতনভাবে মুক্তি চরিত্রটি নিয়ে এমন কিছু ভাবেনি। ‘তালাশ’-এ অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র। আমার একজন সূত্রধরের প্রয়োজন ছিল। তাও মনে হয় উপন্যাসের সেকেন্ড ড্রাফটের সময় প্রয়োজনটা অনুভব করি। তখন দেখতাম, যারা বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তারা নিজেদের ট্রমার কথা খুব লিখতেন। তাদের সাক্ষাৎকার পড়ে কখনো কখনো মনে হতো, রেইপ সারভাইভারের ট্রমার চেয়েও তাদের ট্রমা বেশি। আমি তখন ঠিক করলাম, মুক্তিকে এ রকম আশকারা দেওয়া যাবে না। সে বিনিদ্র রাত কাটালেও তার দুঃখ-কষ্ট কখনো ভুক্তভোগীর দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে যেতে পারে না। সে গল্পের প্রয়োজনে আসবে, আবার চলে যাবে। আড়ালেই থাকবে বেশির ভাগ সময়। এক কথায় তাকে দূরে দূরে রাখছিলাম। তাই হয়তো সে দূরবর্তী সময়ের অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ না-দেখা প্রজন্মের পাঠকের আয়নায় নিজেকে ধরা দিচ্ছে।
তালাশে অনেকগুলো চরিত্র। এসব চরিত্রের ভাবচিন্তা আলাদা। নানা রকম এসব চরিত্রের মধ্যে মরিয়ম একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে বেশ সোচ্চারও। এই চরিত্রটিকে আপনি ঠিক কীভাবে বিকশিত করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। লেখকের সত্ত্বা এখানে কতটুকু মিশে আছে?
‘তালাশ’-এ মরিয়ম প্রধান চরিত্র। সে প্রোটাগনিস্ট উপন্যাসের। চরিত্রটিকে কীভাবে বিকশিত করেছি, তা আপনি উপন্যাসেই দেখতে পাবেন। আলাদা করে আমার বলার কিছু নেই। কোনো ঔপন্যাসিকেরই বোধ হয় থাকে না।
‘তালাশ’ উপন্যাস সত্যিকারেই খোঁজাখুঁজি—তালাশ। তালাশ জনপদে, জনপদের বাইরে, ব্যাংকারে, স্মৃতিতে, বিস্মৃতিতে। বীরাঙ্গনারা যেন শুধু পরিসংখ্যানে আটকে না থাকে। উপন্যাসে তালাশের শেষ নেই, এই অশেষ
চরিত্রের সঙ্গে লেখকের পুরো সত্তা না হলেও কিছু তো মিশে থাকেই। এমনকি চার শ বছরের আগের কোনো চরিত্রের সঙ্গেও লেখকের সত্তা জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন আমার ‘ময়ূর সিংহাসন’ উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের কথা বলা যায়। আমরা নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে কতটুকুই-বা যেতে পারি! আর ‘তালাশ’ তো সে অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। মরিয়ম আমার চেনা আর অচেনা মানুষের মিশেলে তৈরি। সে হয়তো আমার অনেক কিছুই ধারণ করে আছে, যা আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।
যুদ্ধকালে নারী যেভাবে নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়, এই একটি সর্বজনীন বিষয় তালাশে উঠে এসেছে নানা প্রতীকে। এ বিষয়টিই কি এই বইটির ‘এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড’ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন? যেখানে যুদ্ধ একটা সমবোধ বা ইমপ্যাথি তৈরি করেছে।
আপনি যেমন বললেন, ‘এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড’ পাওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা থাকতে পারে। ‘তালাশ’ সম্পর্কে জুরি বোর্ডের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, তারা বলেছেন—‘আমরা বিশ্বাস করি যে, উপন্যাসটি আমাদের সময়ের এশীয় লেখকের অন্যতম সেরা নারীবাদী ও যুদ্ধবিরোধী ডকু-উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার। আমাদের সময়ের যন্ত্রণা ও সাহসের দলিল।’ ‘তালাশ’কে তারা তুলনা করেছেন সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচের ‘দি আনওম্যানলি ফেইস অব দি ওয়ার’, রুথ ক্লাগারের ‘স্টিল অ্যালাইভ’ বা মার্থা হিলারের ‘আ ওম্যান ইন বার্লিন’-এর সঙ্গে। ‘তালাশ’-এর শেষ অধ্যায়ে পৃথিবীর গৌরব, প্রত্যাশা পেছনে ফেলে মরিয়মের যে প্রস্থান, এ সম্পর্কে বিচারকরা বলেছেন ‘এটা সমসাময়িক সাহিত্যের অন্যতম সাবলাইম সীন, মহিমাময় দৃশ্য।’
উপন্যাসটির একটি অসাধারণ দিক প্রতীক ও সংকেতের মাধ্যমে নির্যাতনকে তুলে ধরা। আপনি এই প্রতীক বা সংকেতে কেন নির্যাতনকে তুলে আনলেন?
প্রতীক, রূপক বা মেটাফোরের আশ্রয় না নিয়েও সাহিত্যে ট্রমা বা নির্যাতন তুলে ধরা যায়, এমন উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে। তবে ‘তালাশ’-এ সরাসরি ভায়োলেন্স না দেখিয়ে যুদ্ধের বিভীষিকাময় স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে তা সহায়ক হয়েছে। সহায়ক হয়েছে কখনো আলো-আঁধারি দৃশ্য রচনায়, কখনো-বা বাড়তি একটা অর্থ দিতে, যা কখনো কখনো বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যায়।
ইতিহাস, বিষয় এবং চরিত্র এই তিনটির মিশেল আমরা দেখি তালাশে, তবে এখানে বিষয়টিই বেশি মুখ্য। আপনি কি এ বিষয়টাই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন?
এ তিনটির মধ্যে মনে হয় ইতিহাসের ভূমিকা ‘তালাশ’-এ গৌণ। বিষয় বা কাহিনির প্রয়োজনে চরিত্ররা এসেছে। আবার উল্টোটাও হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রমিজ শেখের ভূমিকা কী? একটা ছাড়পোকা! কিন্তু আমার বিশ্বাস ‘তালাশ’-এর পাঠক রমিজ শেখকে ভুলবে না। টুকির চরিত্রটা নিয়েও একই কথা বলা যায়।
বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যকর্মই বিশ্বে নন্দিত হতে পারত। অনুবাদ সেভাবে না হওয়ার জন্য আমরা পিছিয়ে আছি, এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?
অনুবাদ হওয়া আমি জরুরি মনে করি। অবশ্যই তা হতে হবে ভালো অনুবাদ। তখন অনেক সাহিত্যকর্ম না হোক, কিছু নিশ্চয় বিশ্বনন্দিত হবে।
এই যে মুক্তিযুদ্ধ বা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় সাহিত্য কতটুকু ধারণ করবে? সাহিত্যের দায়ইবা কতটুকু ইতিহাস অথবা ইতিহাসের বিপর্যয়কে তুলে আনার?
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখতেই হবে বা এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের দায় রয়েছে, আমি তা বলব না। কিন্তু সাহিত্য এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সাহিত্য যুদ্ধের ইতিহাসের বাঁধা-ধরা ছক ভেঙে দিয়ে এর বিস্তার ঘটাতে পারে। না হলে তো অনেক নিগ্রহের কাহিনিই বাদ পড়ে যায়, খারিজ হয়ে যায়। ইতিহাসের এ ইচ্ছাকৃত ভুলটুকু সাহিত্য ধরিয়ে দিতে পারে। ফাঁকগুলো পূরণ করতে পারে। এককথায় ইতিহাসের বাকহীনদের মুখে ভাষা দিতে পারে সাহিত্য।