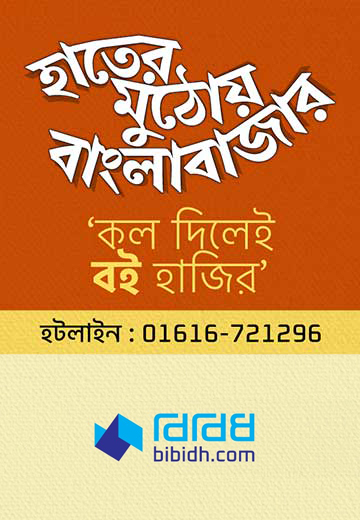আমাদের সত্তার সঙ্গে ভাষা যুক্ত থাকার কারণে আমাদের জীবন ও জগৎবিষয়ক ধ্যানধারণাও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার রূপ ধারণ করে। তবে জীবন ও জগৎ নিয়ে কিছু কিছু ধারণা আমাদের একই মাত্রায় থাকে, যার ফলে সমাজে আমরা একই সঙ্গে চলতে পারি। মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং মানুষের যৌথ মনস্তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে জগৎ ও জীবন-সম্পর্কীয় কিছু স্বতঃসিদ্ধ ধারণা মানুষের মনে যৌথভাবে অবস্থান করে। এমন যৌথ মনস্তত্ত্ব না থাকলে আমরা সামাজিক মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে পারতাম না। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমাদের যৌথ মনস্তত্ত্বই তৈরি করেছে আমাদের সার্বিক চেতনাকাঠামো বা প্যারাডাইম (Paradigm)। সাহিত্য-সৃষ্টির দর্শন বা সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক যেকোনো আলোচনা করতে গেলে বস্তু, ধারণা কিংবা বিষয়ের সঙ্গে ভাষাচিহ্নের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, আর ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ক আধুনিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে সস্যুরের ভাষাতত্ত্বকে উপস্থিত করতে হয়। সস্যুর ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ তার নিজস্ব অবচেতনে ভাষা-সম্পর্কীয় যে সহজাত উপলব্ধি বা নিয়মসমূহকে গ্রাহ্য করে কিংবা পরস্পরের মাঝে ভাব আদান-প্রদানের জন্য ভাষার যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা মানবসমাজের ওপর ক্রিয়াশীল, তাকে সস্যুর ল্যাগ বা ভাষামূল হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভাষাচিহ্ন প্রয়োগের ফলে একজন ব্যক্তিমানুষের মনে জগৎ ও জীবন-সম্পর্কীয় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রকাশ পায়, তাকে তিনি বলেছেন প্যারোল বা মুখের ভাষা। ভাষাচিহ্নের জৈবিক সংগঠন আর প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া, যৌথভাবে একটি ভাষাব্যবস্থাকে মূর্তরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করে এবং এ কারণে ভাষা কিংবা সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় সস্যুর কর্তৃক উল্লিখিত ভাষার এই মৌলিক উপাদান দুটোর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
ধ্রুপদি দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাষা হলো সময় ও সভ্যতার সঙ্গে বেড়ে ওঠা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি শব্দ বিভিন্ন বৈশ্বিক বস্তু, বিষয় বা ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ধ্রুপদি ভাষাতত্ত্বে প্রতিটি ভাষাপ্রতীক বা শব্দের বিপরীতে একটি সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের অবস্থান কল্পনা করা যায়, আর ভাষাপ্রতীক বা শব্দসমূহের সঙ্গে বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্কও একটা সহজ ও সরল সমীকরণ দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। সমীকরণটি হলো : ‘ভাষাপ্রতীক বা শব্দ = বস্তু বা বিষয়’। সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে উপরিউক্ত সমীকরণটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, কারণ কোনো শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রত্যক্ষভাবে কোনো বস্তু বা বিষয়কে উপস্থাপন করে না। একটি শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রকৃতপক্ষে শুধু একটি চিহ্নকে নির্ধারণ করে, আর এই চিহ্নের উপাদানও দুভাগে বিভক্ত, যাকে দ্যোতক ও দ্যোতিত নামে আখ্যায়িত করা যায়। ভাষা ব্যবহারের সময় কোনো একটি শব্দ উচ্চারিত কিংবা লেখা হলে, একটি চিহ্ন দ্যোতক হিসেবে কোনো একটি বস্তু বা বিষয়কে দ্যোতিত করে, অর্থাৎ একটি চিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান থাকে অনেকটা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সমীকরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব।
সামনে অগ্রসর হতে হলে, আমাদের মাঝে বিরাজমান প্যারাডাইমে পরিবর্তন আনতে হবে। বৈষম্য দূর করতে হবে
সস্যুরের তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষাচিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোতিতের অবস্থান নির্ধারণ করা গেলেও কোনো বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা যাবে না, ফলে ভাষা একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতের ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা সম্পর্ক হিসেবেই উপস্থিত। ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যখন রাস্তায় ট্রাফিক বাতির লাল, নীল ও হলুদ আলো দেখি তখন আমাদের অবচেতনে অবস্থিত ভাষাকাঠামোকেই ‘লাল’, ‘সবুজ’ ও ‘হলুদ’ শব্দচিহ্নকে তিনটি নির্দিষ্ট দ্যোতক ও দ্যোতিতের ধারণা হিসেবে উপস্থিত করে। দ্যোতক লাল রং দ্যোতিত হয়ে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হলো ‘থামো’, দ্যোতক সবুজের দ্যোতিত অর্থ হয় ‘যাও’ এবং একইভাবে হলুদ রঙের দ্যোতিত অর্থ ‘থামবে না যাবে তা বোঝার জন্য অপেক্ষা করো’। উল্লিখিত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের সঙ্গে বাস্তব অর্থে ‘থামা’, ‘যাওয়া’ কিংবা ‘অপেক্ষা করার’ কোনো সম্পর্ক নেই, বরং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে রঙের সময় ও অবস্থানকেন্দ্রিক দ্যোতনার সঙ্গে। ভাষাচিহ্ন সৃষ্ট দ্যোতক-দ্যোতনা ও দ্যোক-দ্যোতনার অর্থও সব সময় স্বেচ্ছাচারী, যেমন দ্যোতক লাল শব্দটি দ্যোতিত হয়ে বোঝাতে পারে যুদ্ধ, রক্ত কিংবা সিঁদুরকে, দ্যোতিত সবুজের অর্থ হতে পারে যৌবন, শান্তি, বসন্ত কিংবা ফসলের খেত আর দ্যোতক হলুদ রঙের দ্যোতিত অর্থ নির্ধারণ করতে পারে জন্ডিস রোগ কিংবা চৈত্রের রোদে পুড়ে যাওয়া কোনো এক দুঃসময়কে।
১৯৬৬ সালে আমেরিকার জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে জাক দেরিদা Structure, Sign and Play in the Discourse of Heman Science শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা তৎকালীন ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। দেরিদার প্রবন্ধের বিষয় ছিল প্লাতো ও তৎপরবর্তী ধ্রুপদি পাশ্চত্যদর্শনের বিভিন্ন অধিতাত্ত্বিক ধারণাসমূহের ভাষাকাঠামোগত বিশ্লেষণ, যেগুলোকে দেরিদা যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা বলে আদৌ মনে করেননি। প্লাতো ও তৎপরবর্তী সব দর্শনে ‘অহংক’ মুখ্য হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় বিভিন্ন দর্শনতত্ত্বে ও প্রকল্পে অহং-এর অবস্থান ও ধারণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল কিছু আপাতযৌক্তিক বর্ণনা ও উপস্থাপনার। অহংকেন্দ্রিক এই দর্শনতত্ত্বে কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের বিশ^বীক্ষণজাত যৌক্তিক অনুভূতির ভাষাভিত্তিক বিবরণ থাকলেও, তা আমাদের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি; দেরিদার এ বিশ^াস আমেরিকায় একটি নতুন সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের সৃষ্টি করেছিল, যা বিনির্মাণ নামে পরিচিতি লাভ করে। দেরিদার বিনির্মাণবিষয়ক দর্শন উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে উল্লেখ্য, উত্তর-কাঠামোবাদ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে না। সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ভাষাব্যবস্থার সঠিক ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়ে উত্তর-কাঠামোবাদ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সঠিক পথে উত্তীর্ণ বা বিস্তারিত করে মাত্র। জাক দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শনকে বিশ্লেষণ করার জন্য সস্যুরের ভাষাবিজ্ঞান উপস্থাপন করা আবশ্যক, কারণ ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যই ‘অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের’ যুগ্ম-বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে অহং-সত্তাকে উপস্থিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে। সস্যুরের মতে, ভাষা কোনো বস্তু বা বিষয়ের অর্থ তৈরি করে না, বরং বিষয় বা বস্তুর অর্থকে উদঘাটন করাই হলো ভাষার মূল কাজ। এ তত্ত্বটিকে গ্রহণ করে বলা যায়, ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই অবস্থান করে বস্তু বা বিষয়ের অর্থ। সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে এ-ও বলা হয় যে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষাচিহ্ন বা শব্দ, ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন অন্যান্য-ভাষাচিহ্নের সঙ্গে তুল্য হওয়ার পরই অর্থবোধক হয়। অর্থাৎ আমরা যখন উচ্চারণ করি ‘মানুষ’, তখন তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য, ‘যেহেতু, মানুষ গাছ নয়, বাঘ নয়, পাহাড় নয়, নদী নয় সেহেতু মানুষ অর্থ মানুষ’, এমন একটা তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন নীতি ক্রিয়াশীল থাকে। দেরিদা, সস্যুরের এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করলেও, তত্ত্বটির বিস্তার ঘটান। দেরিদার ধারণায়, কোনো একটি ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন ভাষাচিহ্নের তুলনামূলক অবস্থান-বিশ্লেষণই মানুষকে জীবন ও জগৎসম্পর্কীয় অর্থ প্রদান করে। অর্থ উদ্ধারের এই প্রক্রিয়ায় মানবিক চেতনার ক্রিয়াই থাকে মুখ্য, যার ফলে জগৎ ও জীবনবিষয়ক অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষ তার উপস্থিতি বা অস্তিত্বকে গ্রাহ্য করে তৈরি করে এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ। অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগতের স্রষ্টা মানুষ ‘আমি আছি তাই সবকিছুর অর্থ আছে, সবকিছুর অস্তিত্ব আছে’, এমন একটা উপলব্ধি বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে বিস্তার করে তার সমস্ত চিন্তার জাল। দেকার্ত তার বিখ্যাত উক্তি, আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি আর আমি সন্দেহ করি তাই আমি আছি, দিয়ে অহং-সত্তাকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। দেরিদার মতে, অহং-সত্তাকেন্দ্রিক এই চিন্তা প্রকৃত সত্য কিংবা অর্থকে উদ্ধার করে না, কারণ প্রকৃত সত্য ও অর্থ এক সময়হীন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক-দার্শনিক দেরিদার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মানবিক উপস্থিতি বা অস্তিত্ব ভাষামাধ্যমেই প্রকাশিত, যা কিছু আছে তা অবশ্যই অস্তিত্বশীল কিন্তু অস্তিত্বহীনতার উপস্থিতি না থাকলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্বকেও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের ধারণাকে ভাষাচিহ্নের তুলনাকেন্দ্রিক ‘অর্থ-উদ্ধার-ক্রিয়া’র সমার্থক ভাবা যায়, কারণ যা বর্তমান হিসেবে গ্রাহ্য তা আসলে ‘দ্যোতক/দ্যোতিত’ ক্রিয়াকেন্দ্রিক একটা বিভ্রম হিসেবেই উপস্থিত। একজন মানুষের ‘বর্তমান’ শুধু কিছু ভাষাচিহ্ন এবং তার দ্যোতক/দ্যোতিত নিয়েই অস্তিত্বশীল, যা ক্রমাগতভাবে জটিল হয়ে ‘অস্তিত্বশীল-অনস্তিত্বশীল’ এই যুগ্ম বৈপরীত্যের আওতাধীন একটা ব্যবস্থা হিসেবে অবস্থান করে। দেরিদার মতে, সময় ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে, কারণ বর্তমান বলতে আমরা যা বুঝি, তা ‘বর্তমান সময়কে’ সত্য ও এককসত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে না; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠিত সময়-সংগঠনের একটি তুলনামূলক বিন্দু হিসেবেই বর্তমানের উপস্থিতি।
মানবিক চিন্তন-ক্রিয়া ‘অহং-উপস্থিতি’ থাকার কারণে মানুষ সব সময় তার পছন্দমতো একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করেই চিন্তা-ক্ষেত্রে এগোতে চায়। দেরিদার দর্শনে, কেন্দ্র খোঁজার এই মানবিক প্রবৃত্তিকেই উন্মোচিত করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে। একজন মানুষ যখন তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করে, ঠিক তখনই তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান নেয় ‘আমি’ এবং ‘আমি কেন্দ্রিক’ কিছু ধারণা, যাকে কোনো অবস্থাতেই অহং-অস্তিত্বের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে আমি সত্তা দুটি ভিন্ন মাত্রায়, চেতন ও অবচেতনে বিভাজিত হলেও, চিন্তার কেন্দ্রস্থাপন প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে না। চেতন ‘আমি’-কে বিসর্জন দিয়ে কিছু চিন্তা করতে গেলেও অবচেতন অহং-সৃষ্ট একটা নতুন কিন্তু বিমূর্ত কেন্দ্রের উপস্থিতি মুখ্য হয়ে ওঠে। আসলে মানবিক চেতনা-কাঠামো সব সময় অহংকেন্দ্রিক বিভিন্ন যুগ্মবৈপরীত্যকে কেন্দ্র করেই তার অনুভূতি ধারণার বৃত্ত রচনা করতে চায়। ভালোমন্দ, দেহ/মন, সত্য/মিথ্যা, ঈশ্বর/মানব, ঈশ্বর/শয়তান, মানুষ/পশু, শুরু/শেষ ইত্যাদির মতো অহংকেন্দ্রিক যুগ্ম বৈপরীত্যসমূহকে বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা করতে গেলে, অহং নিজেই ‘অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব’ যুগ্মবৈপরীত্য নিয়ে হয়ে উঠে অস্তিত্বের প্রধান কেন্দ্র বা পরম সত্তা। ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত মানবিক চিন্তায় কোনো কেন্দ্রহীন বিন্দুকে খুঁজে পাওয়া চিন্তাশীল মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবেই অসম্ভব। এখানে উল্লেখ্য, দেরিদার বিনির্মাণ-দর্শন মানবিক চিন্তা বা ধারণার কেন্দ্র রচনার বিরুদ্ধে নয়, কিংবা কোনো কেন্দ্র ছাড়াই চিন্তা করা সম্ভব, এ সিদ্ধান্ত দেয় না। দেরিদা তার দর্শন, চিন্তাকাঠামোর মানবিক উপাদানসমূহকে বিশ্লেষণ করে ভাষামাধ্যমে প্রকাশিত যেকোনো বক্তব্য, বিবরণ, বর্ণনা ও উপস্থাপনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাসহ, অহংচিন্তার কেন্দ্র ও কেন্দ্রের চতুর্দিকে রচিত মানবিক প্রকাশের ক্রিয়া ও বৃত্তকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন যৌক্তিকভাবে।
উল্লেখ্য, একটি ভাষাচিহ্নের দ্যোতক-দ্যোতনা সব সময় ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যান্য ভাষা-চিহ্ন-সেট বা দলের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে অর্থ পায়। আমরা লাল রংকে লাল বলে ভাবি কারণ তা সবুজ নয়, হলুদ নয় কিংবা বেগুনি নয় আর সবুজ রং হলুদ, লাল, বেগুনি কিংবা বর্ণালির অন্যান্য রঙের মতো না হওয়ার কারণে আমাদের কাছে সবুজ হিসেবে অর্থবোধক। ভাষা সব সময় একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন-কাঠামো নিয়ে মানুষের মনে জীবন ও জগৎ-সম্পর্কীয় ভাব প্রকাশ ও সংশ্লেষণ করে থাকে এবং এজন্য ভাষাচিহ্ন ও চিহ্ন-কাঠামোবিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আমাদের সাহিত্য ও সৃষ্টি সম্পর্কে বাস্তব ও সম্পূর্ণ উপলব্ধি দিতে সক্ষম। ভাষাচিহ্ন-সম্পর্কীয় জ্ঞানকে ভাষাচিহ্নবিজ্ঞান বলা হয়, যাকে আমরা ভাষা ও ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে ব্যবহার করতে পারি।
আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমাদের প্যারাডাইম বা চেতনাকাঠামো। যদি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে কোন বিষয়টি সর্বাগ্রে উঠে আসবে? পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একই সমাজে, বহুবিধ শিক্ষা কাঠামো চলমান। যেমন : বাংলা মিডিয়াম স্কুল, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, আলিয়া মাদরাসা আর কওমি মাদরাসা থেকে। এমন বিচিত্র আর বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে জনগণের ভিন্ন মাত্রার চেতনাকাঠামো থাকাই স্বাভাবিক। একই যৌথ-মনস্তত্ত্বে, একই প্যারাডাইমে আমাদের ইতিহাসে ছিল জাতপাত, কুলীন-অচ্ছুত, মেøচ্ছ-মালাউন, শোষক-শোষিত ইত্যাদির মতো বিভাজন। বর্তমানে আছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-চেতনাহীনতা, প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিশীল-প্রগতিশীল প্রগতিশীল, ছুপা-প্রগতিশীল, রাজাকার-নব্য রাজাকার, প্রগতিশীল মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী ইত্যাদির মতো বিভাজন। ভাষাভিত্তিক এই বিভাজনগুলোর প্রেক্ষাপটে আছে সত্য-অসত্য। প্রগতিকে রক্ষা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মাস্তান বাহিনী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিক্রি করে চালু হয়েছে ঘুষ, লুটপাট আর অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সব ধরনের প্যারাডাইমিক ঘটনাকে জায়েজ করার জন্য চালু আছে ভাষাভিত্তিক পণ্ডিতদের বক্তব্য, বিবৃতি, বক্তৃতা আর টকশো। ভাষাচক্রে মানুষ হচ্ছে বিভ্রান্ত, বিচলিত, অবদমিত, আর মানুষ নিস্তেজ হয়ে চুপ করে গ্রহণ করছে সব…!
সভ্যতার নানা উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের কারণে সমাজ অগ্রসর হয়েছে অনেক। কিন্তু সমাজের ভেতরের মানুষের মধ্যে যে একটা পাশবিকতা আছে, অপরাধের প্রতি ঝোঁক আছে। অন্যের সম্পত্তি অধিকারে লোভ আছে। শারীরিক শক্তির প্রতি দুর্বলতা আছে। এর তো কোনো পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে এর ব্যবহারের কৌশল কিংবা মোড়কের। এই অবস্থাতে আমরা সমাজ বা রাষ্ট্র কতটা কার পক্ষে, কার বিপক্ষে ‘ইকুয়াল রাইটস’ প্রতিষ্ঠা করতে পারব? আমাদের মানবিকতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, অন্যের প্রতি বিনয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়পরায়ণতা—এসব কিছুতেই আমরা যদি আমাদের সামগ্রিক চিন্তা এবং চেতনায় এবং ব্যবহারে এর দৃষ্টান্তমূলক দৃষ্টান্ত রাখতে পারি। হয়তো তখনই সম্ভব হবে সমাজে এক ধরনের ইকুয়াল রাইটস কিংবা সমতা আনা অথবা বজায় রাখা। পুরোটা না হলেও আংশিক হলেও। এসব চর্চার সুফল সমাজ এবং রাষ্ট্রে যে ইকুয়ালিটি বয়ে আনবে এবং আনতে পারে, তারও মূল্য কম হবে না। সামনে অগ্রসর হতে হলে, আমাদের মাঝে বিরাজমান প্যারাডাইমে পরিবর্তন আনতে হবে। বৈষম্য দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৈষম্য কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে না।