সৃজনশীলতার সুনিপুণ প্রকাশই শিল্প। সৃষ্টির শুরু থেকেই সৌন্দর্যপিপাসা মানুষের সহজাত। শুধু কি মানুষ? বাবুইয়ের সুন্দর করে বোনা বাসাকেও আমরা শিল্প বলছি। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিচ্ছি। বাবুইকে আমরা নাম দিয়েছি শিল্পীপাখি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—শিল্প তাই, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাগিদ থেকে মানুষকে চালনা করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রয়োজন বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি, যা প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গ এবং যা না করলেই নয়। শিল্পজীবনের অনুষঙ্গ হলেও এটি অতিরিক্ত কাজ যা না করলেও ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু জীবন ও জগতের সৌন্দর্য এবং মননশীলতার চর্চা শিল্প ছাড়া অসম্ভব। যেনতেন করে বোনা কাকের বাসাকে আমরা শিল্প বলছি না। কেন বলছি না? কারণ ওটায় আমরা শিল্পবোধের পরিচয় পাই না। তাতে সৌন্দর্যের আকর্ষণ নেই। ওস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, সৌন্দর্যসৃষ্টিই শিল্পের লক্ষ্য। তাহলে যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, সৃজনশীল না, মানুষের মনকে আকর্ষণ করে না এবং যা কেবল সাধারণ প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়, তা শিল্প নয়। শিল্প সৃষ্টির জন্য চাই অন্তর্গত প্রেরণা, সৃজনআকুলতা, মননশীলতা এবং সাধনা।
শিল্পের জন্মের সঙ্গেই সমালোচনার জন্ম। কোনো শিল্পই সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। যেকোনো শিল্পের গুণাগুণ, উপযোগিতা, বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমালোচকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজ্ঞা, প্রখর শিল্পবোধ আর পরিমিতিবোধ থাকতে হয়।
রবীন্দ্রনাথকে আবার একবার উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। সমালোচনা-বিষয়ে তার চমৎকার একটি বক্তব্য আছে। বক্তব্যটি ছোট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন—‘কাঁচা আমের রস অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে।’
শিল্পের সমালোচনা করার সময় আমাদের উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণদক্ষতা এবং নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিআক্রোশ, ঈর্ষা বা নিন্দাকে সামান্য একটি শব্দেও আশ্রয় দেওয়া যাবে না।
সুতরাং যা-তা লিখে সমালোচনা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। সমালোচনা শিল্পকলার সবচেয়ে কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ। এটি প্রজ্ঞাসাপেক্ষ, জ্ঞানসাপেক্ষ নয়, মনসাপেক্ষ তো নয়ই। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব ফেলে। দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচকতা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথাটাও বলতে দেয় না। শিল্পের সমালোচনা করার সময় আমাদের উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণদক্ষতা এবং নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিআক্রোশ, ঈর্ষা বা নিন্দাকে সামান্য একটি শব্দেও আশ্রয় দেওয়া যাবে না। মনে রাখা ভালো, সমালোচনার সীমা হচ্ছে নিন্দা, সেটিকে অতিক্রম না করাই এর সৌন্দর্য।
এটা সত্য যে, সাহিত্যে সজনীকান্ত দাসীয় সমালোচনা একটা অনৈতিক ভয়াবহতা, ঘৃণা আর বিদ্বেষের মহামারি আমাদের মনেপ্রাণে ছড়িয়ে গেছে। ফলে যত সহজ করেই আমরা বলি না কেন, সমালোচনা জিনিসটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। সম্প্রতি তাই অনেক তরুণ সমালোচনাকে নিন্দা বলে মনে করেন। তারা সমালোচনা চান না। ভয়ের কথা হলো, সমালোচনা যে সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ, এটিও তারা মানতে চান না।

ঢাকায় প্রতিদিনের সংবাদ অফিসে লেখক
সাহিত্য হচ্ছে ভাষাশিল্প। ভাষাই এর বাহন। সাহিত্যে সমালোচকের কাজ হচ্ছে ভাষার সৌকর্য তথা শিল্পের গুণগত মান নির্ণয়। নন্দনতাত্ত্বিকদের মতোই সাহিত্যসমালোকের প্রজ্ঞা থাকতে হয় শিল্পের সব বিষয়ে। একটি বিশেষ মাধ্যমের শিল্পকর্মের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিচার এবং শিল্পের মাপকাঠির নিরিখে গুণগত অবস্থান র্নিণয়ই সমালোচক করে থাকেন। মূল্যায়ন হতে হয় শিল্পকর্মভিত্তিক, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিমূল্যায়নের সুযোগ নেই।
একজন শিল্পীর শিল্পবোধের সঙ্গে সমালোচকের শিল্পবোধ তাল মেলাতে নাও পারে। সেক্ষেত্রে শিল্পী এবং সমালোচকের মনোগত দ্বন্দ্ব উস্কানি পায়। সেজন্যই শিল্পী বা লেখকের সমালোচনা গ্রহণ-উপযোগী একটি মন তৈরি হওয়া জরুরি। শুধু বাইরের কেন, নিজের ভেতরেও একজন সমালোচকের জন্ম দিতে পারা প্রত্যেক শিল্পী তথা লেখকের জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ।
শিল্পের যত রকম শাখা-প্রশাখা আমাদের চোখের সমুখে পাখনা মেলে, এর সবকিছুকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এটি দেখতে, শুনতে বা বুঝতে কেমন? এটি কি নিখুঁত? কতটা নিখুঁত? কেন নিখুঁত? না হলে কেন নয়?
আমরা সাধারণভাবে এসব প্রশ্ন তো করিই। শুধু শিল্প কেন, যেকোনো কিছু নিয়েই আমরা প্রশ্ন করে অভ্যস্ত। তবে সমালোচকের কাজ শুধু প্রশ্ন করা নয়, উত্তরটাও জানিয়ে দেওয়া।
শিল্প-সাহিত্যে সমালোচনার বয়স খুব বেশি নয়। অষ্টাদশ শতকের আগে পাশ্চাত্যেই শিল্পতত্ত্ব বা শিল্পালোচনা আলাদা বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এটি ছিল দর্শনের অংশ। সে সময় জার্মান দার্শনিক বমগার্টেনকে আধুনিক সৌন্দর্যচিন্তার জনক বলা হতো। তারপর জার্মান দার্শনিক জে কে উইংকেলম্যানকে আধুনিক শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প আলোচনার জনক বলে অভিহিত করা হয়।
সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়েই শিল্পচর্চায় মনেনিবেশ করা উচিত। কেননা সমালোচনা মানে নিজের দিকে বারবার মনোযোগী দৃষ্টি ফেলার সুযোগ
ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্প ও সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের ধারণা ও ভাবনায় প্রভাবিত। তবে পশ্চিমের তথা উপমহাদেশীয় পরিমণ্ডলে চলমান আধ্যাত্ববাদী শিল্পদর্শনের বিপরীতে অবনীন্দ্রনাথ ও বরীন্দ্রনাথ রোমান্টিক-ভাববাদী শিল্পভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার বা বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ এ ধারাকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।
আমার মনে হয়, শিল্পের যেকোনো বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে হলে দার্শনিকসুলভ প্রজ্ঞা থাকা জরুরি। কালসচেনতা এবং প্রেক্ষিতজ্ঞানও থাকা চাই। তবে বাংলাদেশে সমকালীন সমালোচনায় নতুনতর দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। এখানে আধুনিক-উত্তরধুনিক চিন্তার প্রয়োগ এবং উত্তর ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে সমসামসয়িক দৃশ্যকলাকে মূল্যায়নের প্রয়াসও আছে। ফলে সমালোচনার বহুমুখি চিন্তনপ্রক্রিয়া এবং কৌশল আমাদের নতুন করে ভাবাচ্ছে।
সম্প্রতি দেশের বিশিষ্ট একজন কবি সমালোচনাকে একেবারেই অগ্রাহ্য বলে প্রচারের পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কী সেই দুই সিদ্ধান্ত? তিনি বলেছেন সাহিত্যের কোনো সমালোচনা হয় না। সাহিত্যের হয় প্রশংসা করতে হবে, নয় নীরব থাকতে হবে। এর প্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমি একটা গল্প বলেছিলাম। গল্পটি এ রকম—
এক দেশে রাজা নির্বাচিত হলেন মি. ফড়িং। ফড়িংয়ের কবিপ্রতিভা আছে। কিন্তু তার সন্দেহ, বাঘ হাতি মোষ সিংহরা তাকে কবি হিসেবে গ্রহণই করবে না। তাহলে কী করা? রাজা আদেশ জারি করলেন, তার কবিতা শুনে সবাইকে প্রশংসা করতে হবে। যে প্রশংসা করবে না, তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সভাসদদের আর উপায় কী?
রাজা লিখে যা-ই শোনান, সবাই সমস্বরে বলেন, মারহাবা! মারহাবা!
এক দিন রাজা তার সেরা কবিতাটি লিখলেন। আসরের মধ্যমণি হয়ে তিনি আবৃত্তি করলেন—‘আমি রাজা, আমার বড় কেউ তো নও/এই রাজ্যের সকল নারীই আমার বউ।’
সাহিত্য হচ্ছে ভাষাশিল্প। ভাষাই এর বাহন। সাহিত্যে সমালোচকের কাজ হচ্ছে ভাষার সৌকর্য তথা শিল্পের গুণগত মান নির্ণয়
সভসদরা দেখলেন, মহাবিপদ। রাজা তো সবার বউ কেড়ে নিচ্ছে কৌশলে। প্রশংসা না করলেও যায় প্রাণ। তারা একবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর বলে দিলেন, মারহাবা।
এদিকে বাড়িতে ফিরে গেলে প্রত্যেক বউ স্বামীদের ঝাড়ুপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।
তার পরদিন রাজা কবিতা পড়লে বাধ্য হয়ে সবাই নীরবতা পালন করলেন। রাজা বললেন, সবাইকে ফাঁসি দাও।
আমার মনে হয়, সে কবি পাগলা রাজার মতোই কথা বলেছেন। অথচ সমালোচনাই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসা শিল্প এবং শিল্পী উভয়কেই মেরে ফেলে। মনে রাখা ভালো, সমালোচনা মানে কোনো শিল্পকে খারিজ করে দেওয়া নয়। বরং সে শিল্প কীভাবে আরো মানোত্তীর্ণ হতে পারে বা পারত, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। অবশ্য সমালোচকের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে সমালোচনার ধরণ বা প্রকৃতি নিয়েও।
প্রকৃত সমালোচনা যেকোনো শিল্পের গুরুত্ব বাড়ায়, বড় পরিমণ্ডলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্দীষ্ট শিল্পশাখাটি নিয়ে নতুন করে ভাববার সুযোগ দেয়। তাতে এর ইতিবাচক প্রচারও বাড়ে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুটো ভয়ের বিষয়—অতিপ্রশংসা আর নিন্দা। নিন্দা তো গ্রহণযোগ্যই নয়, প্রশংসার ক্ষেত্রেও থাকা চাই পরিমিতিবোধ।
সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়েই শিল্পচর্চায় মনেনিবেশ করা উচিত। কেননা সমালোচনা মানে নিজের দিকে বারবার মনোযোগী দৃষ্টি ফেলার সুযোগ। আত্মতুষ্টির অস্বাভাবিক ব্যারাম থেকে মুক্ত হয়ে নিজের প্রকৃত সত্ত্বাকে উন্মোচনের সুযোগ এবং সৃজনসৌন্দর্যের আয়নামুখ বিশ্বাভিমুখে খুলে দেওয়ার প্রবণতাকে সাধুবাদ জানানো।


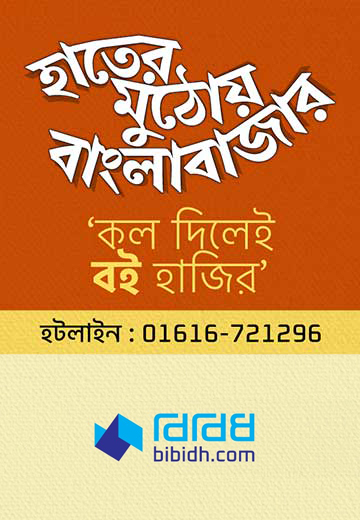
১ comment
পারফেক্ট সমালোচনা। আপনার গদ্য নিয়মিত হোক